“দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ”
এই প্রবন্ধটি লিখতে গিয়ে কিছুটা, – না, কিছুটা না, – খুবই অসুবিধা হচ্ছে এটা অনুমান করে লেখা যাবে না। উচিতও হবে না। তাছাড়া বিষয়টা খুবই সংবেদনশীল! কোনো কিছুর সফলতার কারণ অনেক সময়ই খুব স্পষ্ট, খুবই পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু, গোষ্ঠ ভবনের মত এক টাইটানিক পরিবারের সফলতা কিংবা বিফলতার কারণ নির্ধারণের অনুশীলন ও অনুধাবন করার ধৃষ্টতা যেন আমাদের না হয়! তাছাড়া আমাদের ভবন, গোষ্ঠ ভবন কোন মাপকাঠিতে সফল আর কোন স্টাটিস্টিক প্যারামিটারের নির্ণায়ক সংখ্যায় কতটা পিছিয়ে, তার মানদণ্ড কে নির্দিষ্ট করবে? জ্বরমাপার জন্য যেমন থার্মোমিটার আছে, সেইরকম রক্তচাপ মাপার যন্ত্র, এমনকি অক্সিমিটারও আজকাল বহুল পরিচিত… কিন্তু পারিবারিক সাফল্যের মাপকাঠি বা সঠিক নির্ণায়ন করার জন্য কোন কোন মিটার-যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে? কিভাবে মূল্যায়ন করা যাবে প্রতিবেশী যৌথ পরিবারের সফলতা বা বিফলতা? হয়তো বর্তমান প্রযুক্তির কোন কৃত্রিম বুদ্ধি (AI /ML) মডেল কিছুটা ব্যবহার করা যেতে পারে, সেটার আলোচনা এ পর্বের বিষয় বস্তু নয়… আবার স্বার্থহীনতা, মানবতা, সততা, দান-দয়া-দাক্ষিণ্য সহমর্মিতা, সমবেদনা, স্নেহ -ভালোবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা এইসব ইমোশনাল গুণরাশিকে যদি সত্য সত্যই যদি মূল্যায়ন করা সম্ভব হত তাহলে লেখাটা অনেক সহজ হত!!
মানুষের জীবনধারণের জন্য তিনটি মুখ্য চাহিদা, – থাকার জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়, দুবেলা দুমুঠো খাবার আর লজ্জা
নিবারণের জন্য জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা। তাছাড়া যুগের সঙ্গে চলতে গেলে দরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা। গোষ্ঠ ভবনের যৌথপরিবারে ওই সমস্ত সুযোগ সবই ছিল, যদিও ছিল খুবই ন্যূনতম মাত্রায়। কোনোরকম বিলাসিতা ছিল না। মধ্যবিত্ত, মূলত কৃষিনির্ভর যৌথপরিবারে ধান, গম, আলু, সরিষা ও অন্যান্য তৈলবীজ পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন হত। সারাবছরের খাবার বরাদ্দ রেখেও অনেকটা উদ্বৃত্ত থাকত। ওই উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে যে ক্যাশ টাকা আসত, তা দিয়ে সারাবছরের দোকানদানি, হাট – বাজার, ডাক্তার – ওষুধপত্র ও পরিবারের অন্য সব খরচপত্র মেটানো হত। তাছাড়াও যদি বিশেষ দরকার পড়ত, ছোট কাকা ও চাকুরিরত দাদারা কনট্রিবিউট করতেন। এইভাবে কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে সংসার চলে যেত। আমরা বিশেষ করে ছোটরা কোনোরকম অভাব-অভিযোগ বুঝতে পারতাম না। যদিও শেষের দিকে বাড়ির কর্তা মেজ জ্যাঠামশাইকে মাঝে মাঝে বকাবকি করতে শুনতাম। বিশেষ করে বড়দাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতেন –“তুই আর জগন্নাথ একটু বেশি টাকা না দিলে এত বড় সংসার কি করে চালাই বল তো?” এই সময় আমরা তিন ভাই ও দুই বোন খুবই অসুবিধায় পড়ি। আমাদের বই খাতা কেনার মতো কোনো পয়সা দিতে পারতেন না। স্কুল ও কলেজের ফী দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সুধাংশুদা তখন বি. এস সি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র আর আমরা সব হাই স্কুলে পড়ি। আমাদের দুই দিদি তখন শ্বশুরবাড়িতে। আমরা এই প্রতিকূলতাকে কীভাবে কাটিয়ে এগিয়েছিলাম তা একমাত্র আমাদের বিধবা মা আর ঈশ্বরই জানেন।
যে কোনো যৌথপরিবারের এক অলিখিত শর্ত হল পরিবারের সমস্ত সদস্যের খাওয়াদাওয়ার অন্নভোগ একই রান্নাঘরে হবে, সবাই একসঙ্গে বসে আনন্দ সহকারে উপভোগ করবে। একই ছাদের আশ্রয়ে বসবাস করবে। জামা কাপড় ও জীবনযাত্রার মান কমবেশি একই রকম হবে। সকলের সুখ সকলে মিলে উপভোগ
করবে সকলের দুঃখ সকলে বেঁটে নেবে। গোষ্ঠ ভবনের যৌথপরিবারও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তবে, এই বিশাল পরিবারকে বিভিন্ন সময়ে অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে।
রঘুনাথ পালদের যৌথপরিবার
অথচ গোষ্ঠ ভবনের জ্ঞাতি পরিবার রঘুনাথ পালদের যৌথপরিবার খুবই উন্নতি করেছিল। তাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের অনেক সদস্য বাইরে-বাইরে থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক অনুষ্ঠানে ও পালাপার্বণের সময় সবাই গ্রামের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। যৌথপরিবারের পরিকাঠামোটি এখনো অটুট। এই যৌথপরিবারের সেজ কর্তা কানাই পালের কর্তৃত্ব ও অবদান অতুলনীয়। পাঁচ ভাইয়ের যৌথপরিবারের বাড়ির বড়কর্তা রঘুনাথ পাল খুবই নরম প্রকৃতির, স্নেহপ্রবণ, যেন মাটির মানুষ। কাব্য ও উপন্যাস পড়তে ভালোবাসতেন। তাঁর সমস্ত ভাইদের খুব স্নেহ করতেন, যদিও সেজ ভাই কানাইয়ের উপর অতিরিক্ত ভরসা করতেন। বয়সে ছোট হলেও তার সমস্ত মতামত ও সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিতেন। ভাইদের মধ্যে কোনো মতের আপাত-অমিল ছিল না। কানাই পাল ছিলেন প্রকৃতপক্ষে যৌথপরিবারের কর্ণধার। শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন। কেউ ওনার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পেত না। ছোট ভাই গুণধর পালের সঙ্গে ওনার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। গুণধর বাবু ছিলেন পি. ডব্লু. ডি অফিসার। নিজের স্ত্রী আর দুই মেয়ে নিয়ে বাইরে বাইরে থাকতেন। মাঝেমধ্যেই সপরিবারে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন। আনন্দ-উৎসবের রোল পড়ে যেত। সকলের সঙ্গে বসে তাস খেলতেন, আধুনিক ও শহুরে আড্ডা জমাতেন গ্রামের মাটিঘরে বসে। মেজ কর্তা শশধর পাল একটু সৌখিন ধাঁচের ব্যক্তি; যাত্রাভিনয় করতে ভালোবাসতেন, বেশিরভাগ সময় রাজা, বাদশা কিংবা নবাবের চরিত্রে। সারাদিন নিজের মনে রিহার্সাল দিতেন।
সেজভাই ও দাদার সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করে তিনি একটা কৃষি সারের দোকান খুলেছিলেন, কোলেপুকুরে বাস রাস্তার ধারে। সেজ কাকার পরের ভাই, বলাই পাল কৃষিকাজ ও চাষবাস দেখাশোনা করতেন। পাঁচজন মেয়ের বাবা, যৌথপরিবারে কিছুটা বিন্দাস হয়ে থাকতেন। পারতপক্ষে, কানাই পাল সবার সঙ্গে যুক্তি-আলোচনা করে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতেন ও ভাই-ভাইপো ও অন্য সদস্যরা সব মেনে নিতেন।
কানাইবাবু তাঁর ছেলে-মেয়ে আর ভাইপো-ভাইঝিদের সকলের জন্য শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। নিজের মেয়েদের ও ভাইঝিদের সুপাত্রে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।
বড় ভাইপো দেবিদাস পাল প্রচন্ড মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বালি দেওয়ানগঞ্জ হাই স্কুলের শিক্ষক সেজ কাকার তত্ত্বাবধানে তিনি আই. এস সি / পি. ইউ পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করেন, প্রথম ডিভিশনে পাশ করা সেই সময় বিরাট কৃতিত্বের ব্যাপার। ঘটনাচক্রে ছোট কাকা গুণধর পাল তখন কলকাতার নিকটবর্তী স্থানে পোস্টিং ছিলেন। সন্তানসম ভাইপোর দেখাশোনার ভার তিনি অনেকটাই নিয়েছিলেন। মেধাবী ভাইপো তার ছোটোকাকার পরামর্শে যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি হন। পাশ করার পর দেবিদাস পাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে বড় পোস্টে চাকরি করেন।
এদিকে পরের ভাইপো রবি পাল প্রচন্ড পরিশ্রমী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ছোট কাকা ও বিশেষ করে বড়দার কাছে অনুপ্রেরণা পান। আরামবাগ কলেজ থেকে পাশ করে তিনি উচ্চশিক্ষার দিকে মন দেন। গ্রামের বাড়ি ছেড়ে কলকাতার যাদবপুরে থেকে উচ্চতর পড়াশোনা করবেন ঠিক করেন। একটু একরোখা প্রকৃতির রবি পাল বাবা ও সেজ কাকাকে বুঝিয়ে যাদবপুরে আসেন। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট ও অসুবিধা হলেও পরের
দিকে টিউশন পড়ানো শুরু করেন। দাদা দেবিদাস পাল কিছুটা সাহায্য করলেও তিনি মনের জোরে ও পরিশ্রম করে পড়াশোনা চালিয়ে যান। পি এইচ. ডি করে কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তীব্র ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণ করেন। তখনকার দিনে আরামবাগের আশেপাশে খুব কম মেধাবী ছাত্র বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেত।
রবি পাল বুঝেছিলেন ও নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন আরামবাগ ও তার আশেপাশে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব সীমিত। এদিকে কলকাতা ও শহরতলিতে তখন অনেক সুযোগ। বিশেষ করে গ্রামবাংলা ও মফস্বলের সাধারণ মেধার অনেক পরিশ্রমী ছাত্র কলকাতায় এসে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে বেশ উন্নতি করছে ও সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। গ্রামের ভালো ভালো ছাত্ররা ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চান্স না পেলে সাধারণত ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বা গণিতে অনার্স পড়ত। সাধারণ মানের ছাত্ররা বায়ো-সাইন্স কিংবা পিওর সাইন্স নিয়ে পাস কোর্সে পড়ত। নিম্ন মেধার ছাত্ররা আর্টস কিংবা কমার্স নিয়ে পড়ত। তখনকার দিনে গ্রামের ছাত্রদের পথ দেখাতেন নিজের স্কুলের শিক্ষকরা কিংবা অভিভাবকরা। কোনো এক স্কুলের মাস্টারি বা একটা সাধারণ চাকরির স্বপ্ন দেখত গ্রামবাংলার ছাত্রছাত্রীরা। যাতে পারিবারিক ব্যবসা বা চাষবাস করতে না হয়। কিন্তু রবি পাল এই মধ্যবিত্ত মানসিকতায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি তাঁর পরের ভাই শঙ্কর ও স্বপনকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। যাতে তারা নিজেদের মতো শিক্ষা ও কর্মের সুযোগ সন্ধান করে নিতে পারেন। ভাইয়েদের থাকা খাওয়ার খরচ মেটানোর জন্য তিনি আরো দুয়েকটা বেশি টিউশন করতে শুরু করেন। ভাইয়েদেরও টিউশন করার পরামর্শ দেন।
ছেলেদের রান্না-খাওয়া ও ঘরোয়া পরিবেশ তৈরি করার জন্য রবি-শঙ্করের মা, মানে আমাদের মেজ জেঠিমা যাদবপুরে তাদের
সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। ভাই শঙ্কর ক্রমে ক্রমে উচ্চশিক্ষার পর কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ততদিনে যাদবপুরের গড়ফা মেন রোডের দু কামরার ভাড়া-নেওয়া ফ্ল্যাট পালবাড়ির একটা আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল, শহরের মধ্যে একটা ঠিকানা।
কানাইবাবুর ছেলে তারক ও ভাইপো তপন একই বয়সী যমজ ভাইয়ের মতো। দুজনই গ্রামের মেধাবী ছাত্র। কানাইবাবু দুজনকেই যত্নের সঙ্গে বড় করেন। নিজে স্পেশাল কোচিং দিতেন দুজনকেই। ভেবেছিলেন ডাক্তারি পড়াবেন। উচ্চ মাধ্যমিকে দুজনেই ভালো নম্বর পেয়ে সেই যাদবপুরের ঠিকানায় হাজির হয়। এখানেও আমাদের রবিদার চিন্তা ও সিদ্ধান্তর বেশ বড় ভূমিকা ছিল। কানাইবাবু ও বাড়ির সকলে চেয়েছিলেন তারক – তপন আরামবাগ কলেজে কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করুক। কিন্তু আধুনিক মনের রবি পাল অনেক খোঁজখবর নিয়ে ও চিন্তাভাবনা করে স্থির করেছিলেন যে তারক – তপন জিওলজি নিয়ে পড়বে, যাদবপুরে। জিওলজির ব্যাপারটা কানাইবাবুর কাছে অজানা ছিল। ছেলেদেরকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পাঠাতে রাজি ছিলেন না কানাইবাবু। কিন্তু স্থিরমতি ও যুক্তিবাদী ভাইপো রবি একপ্রকার জোর করেই তারক – তপনকে জিওলজিতে ভর্তি করেন। ভাইয়েদের নিয়ে তাদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার আর এক স্নেহের সংসার তৈরি করেন। সেজ কাকা কিছুটা পয়সা পাঠালেও তারক-তপনকে রবিবাবু বাকি সাপোর্ট দিতেন। দুজনেই যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে জিওলজি নিয়ে পড়াশোনা করে। মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করে একই গাইডের আন্ডারে পি এইচ. ডি করে। উচ্চশিক্ষা শেষ করে সরকারি চাকরি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে যায়। ছুটিতে কিংবা সুযোগ হলেই চলে আসে মেজদার আশ্রয়ে, ঠিকানা সেই গড়ফা রোডের ফ্ল্যাট। ছেলেদের খাওয়াদাওয়ার সমস্ত ভার সেই আমাদের সদা-হাসিমুখের স্নেহময়ী মেজ কাকিমা। কানাইবাবুর
আরো দুই ভাইপো, কাশীনাথ এবং সবচেয়ে ছোট ভাইপো দিপু, বেশ কয়েকদিন গড়ফা লেনের ওই ঠিকানায় আশ্রয় পেয়েছিল। কাশীনাথ পাশ করে কলেজে অধ্যাপনা শুরু করে, মেজ কাকিমার আশীর্বাদে ওই একই ফ্ল্যাটে থেকে দিপু, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টিং পাস করে। কানাইবাবুর যৌথ পরিবারের সন্তানদের সফলতায় মেজকাকিমা ও গড়ফা লেনের ওই ফ্ল্যাটটির গুরুত্ব অপরিসীম। তবে পালবাড়ির সব ছেলেই কমবেশি মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন। যার ফলে সবাই উচ্চশিক্ষায় সফল হন ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তাছাড়া এখানে এক অদ্ভুত ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়। কানাইবাবুর দুই বড় দাদা তাদের সেজ ভাইকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে। গুণধরবাবু দাদাদের আশ্রয়ে থেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন এবং পরবর্তীকালে ভাইপো দেবিদাসকে সাহায্য করেন। পরের দিকে রবি পাল একদিকে যেমন দাদার কাছে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন অন্যদিকে তার ছোট কয়েকজন ভাইদের স্নেহ দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে ও অত্যধিক পরিশ্রম করে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বড় করেছেন। তারপর তপনদা- তারকদাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে জ্যাঠতুতো ভাই কাশীনাথ ও দিপুও কলকাতায় আসে, যদিও সেজকাকা কানাইবাবু পয়সা পাঠাতেন। যে কোনো যৌথপরিবারেই এই একে অপরের জন্য চিন্তা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া পরিবারের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক সাফল্যের প্রধান চাবি কাঠি। রঘুনাথ পালদের যৌথপরিবার তার উদাহরণ রেখে গেছে।
মিতভাষী, প্রগতিবাদী ও স্নেহশীল পাড়ার দাদাদের যাদবপুরের সংসারে অনেকবার আসার সুযোগ হয়েছিল গোষ্ঠ ভবনের ওই পেটরোগা ছেলেটার। প্রথম আসার সুযোগ হয় ১৯৮৩ সালে, রামকৃষ্ণ মিশনে থাকাকালীন। তাপর বি.ই কলেজে ভর্তির আগের দিন। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কাউন্সেলিংয়ের সময়। তারপর নিয়মিত যাতায়াত হয় ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত।
রঘুনাথ পালের যৌথপরিবারের ওই বাহ্যিক সাফল্য পরিবারের সবাইকে কি খুব সুখী করতে পেরেছিল? শুধু তাই নয়, রঘুনাথ পালের ভাইপোরা একে একে বিয়ে-সংসার করে যৌথপরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। সব ছেলেমেয়ে বাইরে থেকে যায় নিজের নিজের সংসার নিয়ে। রঘুনাথ পালের যৌথপরিবার হয়ে ওঠে বয়স্ক কাকা-কাকিমা, জ্যাঠা-জ্যাঠাইমাদের আবাসন। তাঁদের কোনো দরকার পড়লে, বিশেষ করে ওষুধপত্র, ডাক্তার কিংবা হসপিটালে নিয়ে যেতে হলে ডাক পড়ত পাশের বাড়ি গোষ্ঠ ভবনের সুকুমার পালের! এটা কী ধরনের যৌথপরিবারের ভাগ্যের পরিহাস? এটা কী ধরনের সার্থকতা ? এটাই বোধ হয় যৌথপরিবারের উপর আধুনিক শিক্ষা ও আধুনিক জীবনযাত্রার কুফল। কানাইবাবুর ওইসব উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত ভাই ও ভাইপোদের তাদের ফেলে আসা গ্রামের যৌথপরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বিশেষ কোনো ভূমিকা নেয়া সম্ভবপর ছিল না। তাদের ভূমিকা অনেকটা আত্মীয়স্বজনের মতো হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি কলকাতার আশেপাশে বসবাসকারী ভাইয়েদের মধ্যেও খুব বেশি যোগাযোগ ছিল না। থাকা সম্ভবপরও নয়। সকলের নিজের নিজের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। আলাদা আলাদা সংসারের বৈশিষ্ট্য ও প্রায়োরিটিও আলাদা। পরে অবশ্য এক ভাইপো স্বপন গ্রামে ফিরে আসে এবং বিয়ে করার পর ওই একই যৌথপরিবারে বসবাস শুরু করে। গুরুজনদের দায়দায়িত্ব স্বীকার করে। বয়স্ক গুরুজনদের একমাত্র আশ্রয় তিনি। যৌথপরিবারের একমাত্র যষ্ঠি।
শুরু থেকেই গোষ্ঠ ভবনকে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। গোষ্ঠ ভবনের কাছে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ছিল ঠাকুমার বড় ছেলে, আমাদের বড় জ্যাঠামশাই ঈশ্বর ভাগবত পালের অকালমৃত্যু। তিন নাবালক সন্তানের বাবা ভাগবত পাল মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বড়দার বয়স তখন পাঁচ বছর। অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না থাকায় বড়দার বড় হয়ে
ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ছাড়তে হয়। বড়দি ও সেজদি খুব মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও পড়াশোনা বেশি দূর এগোয়নি। এত ছোটবেলায় বিয়ে না হলে ওনারা নিশ্চিত উচ্চশিক্ষায় সফল হতেন। ছোট কাকা বাড়ির বাইরে বাইরে চাকরিরত থাকায় ভাইপো-ভাইঝিদের যথাযথ গাইড করার সময় ও সুযোগ পাননি। ছোট কাকার জীবনে সবচেয়ে বড় ধাক্কা ওনার প্রথম পুত্রের (প্রশান্ত পাল ) মৃত্যু। তারপর থেকে ছোট কাকা বেশ উদাসীন হয়ে পড়েন। শুনেছি ছোট অবস্থাতেই প্রশান্ত পাল খুব বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে ছিল। বেঁচে থাকলে হয়তো গোষ্ঠ ভবনের স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হত। তার পর হঠাৎ একদিন গোষ্ঠ ভবনের আকাশে ঘোর মেঘ ঘনিয়ে আসে। সেজ ছেলে ঈশ্বর গোবিন্দ পালের মৃত্যু। গোষ্ঠ ভবন আরো একবার অভিভাবকহীন হয়। কয়েকজন নাবালক ছেলে মেয়ে পিতৃহীন হয়।
এই মৃত্যু শুধু যৌথপরিবার থাকাকালীন নয়, এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী ; সেপারেশনের পরও ঈশ্বর গোবিন্দ পালের পরিবার ছিল যথার্থই অভিভাবকহীন। বিধবা মা তার কয়েকজন নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার শুরু করেন। ঈশ্বরের অসীম কৃপায় দুই সদ্য গ্রাজুয়েট ছেলেকে বিধবা মা তাঁর সংসারের কাজে যোগ দিতে বলেন। পেটরোগা ছোট ছেলেটা সেপারেশনের কিছুদিন পরেই রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমে সুযোগ পেয়ে চলে যায়। তবু তার মনে জ্বলজ্বল করতে থাকে গোষ্ঠ ভবনের স্মৃতি। ছুটির পর বাড়ি এলেই তার কাছে সেই যৌথপরিবার। গোষ্ঠ ভবনের প্রত্যেকটা ঘরে তার অবাধ যাতায়াত। কাকিমা-জ্যাঠাইমাদের অপরিসীম স্নেহ, দাদা-দিদি-ভাই-বোনেদের সবার ভালোবাসা, এখনো নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে হয়। আলাদা আলাদা রান্না হলেও, এখনো কেন যেন মনে হয় আমি যৌথ পরিবারেই এসেছি। এটাই আমার বাড়ি। এটাই যেন আমার কাছে স্বর্গ! এখানেই যৌথপরিবারের সার্থকতা!
ছোটখাটো পারিবারিক সমস্যা সব পরিবারেই থাকে। তবে গোষ্ঠ ভবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক সমস্যা। এই
সমস্যার জন্যই গোষ্ঠ পালের নাতিনাতনিরা শিক্ষার সুযোগ পায়নি। কয়েকজন ছোট ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছিল। সময়মত যথাযথ সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়নি।
গোষ্ঠ পালের চার ছেলের পরিবার নিয়ে যৌথ সংসার শুরু থেকেই অনেক গুরুভার বয়ে এসেছে। নীরবে নিঃশব্দে কতশত দায়দায়িত্ব পালন করে এসেছে, সে কথা আজ ইতিহাসও ভুলতে বসেছে! পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনায় টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি ভেসে ওঠে। এই পরিবারে জন্ম-হওয়া ও বেড়ে-ওঠা পেটরোগা ছেলেটা তার গর্বের সুতো দিয়ে ওইসব স্মৃতিগুলোকে কুড়িয়ে গেঁথে-গেঁথে স্মৃতির মণিহার তৈরি করে গোষ্ঠ ভবনের ফটকে পরাতে চায়। তার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস,- যাতে গোষ্ঠ ভবনের অস্তিত্ব ও মহিমার সংবাদ পরিবারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বেষ্টনী ছেড়ে, দেশ-কাল পাড়ি দিয়ে এমনকি সুদূর বিদেশেও প্রচারিত হয়, এবং সেইসঙ্গে গোষ্ঠ ভবনের ইতিহাস, পরিবারের চরিত্র, চালচিত্র, আনন্দ-অনুষ্ঠান, পারিবারিক পূজা-উৎসব, সংস্কৃতি, তার পাড়াপ্রতিবেশী ও গ্রাম, মাঠ, ঘাট ইত্যাদি নিয়ে একটি ছোট্ট অকিঞ্চিৎকর স্মারক পুস্তিকা গোষ্ঠ ভবনের পাদমূলে অর্পিত হয়।
তথ্য ও ঘটনা : তপন পাল ও সচ্চিদানন্দ পাল












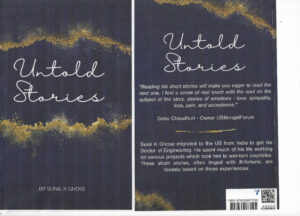


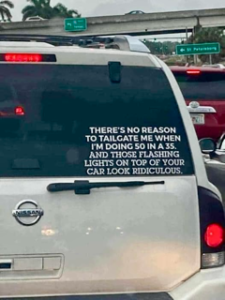
Comments »
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Leave a comment